বাংলাদেশের নৈতিক ও সামাজিক সংকট: ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কী বার্তা বহন করে
- শহীদ রায়হান, চলচ্চিত্র নির্মাতা,লেখক।
বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও সমাজের গভীরে একাধিক সংকট বিরাজ করছে। সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক এসব সংকট জাতির অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকি স্বরূপ। জনসংখ্যার একটি বড় অংশই তরুণ; সাম্প্রতিক আদমশুমারিতে দেখা গেছে দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭০ মিলিয়ন (১৬.৯৮ কোটি) এবং এর প্রায় ২৮% এরই বয়স ১৫-২৯ বছরের মধ্যে। আবার মোট জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি ১৮ বছরের নিচে শিশু-কিশোর। এই বিপুল যুব ও শিশুকিশোর জনগোষ্ঠীই দেশের আগামীদিনের চালিকাশক্তি, যাদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ এবং রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। কিন্তু দুর্নীতি, ন্যায়বিচারের অভাব, শিক্ষার মান-সংকট ও নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রভৃতি সংকট আগামী প্রজন্মের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আন্তর্জাতিক সূচকগুলোর দৃষ্টিতেও এসব সংকট স্পষ্ট: উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশের স্কোর মাত্র ২৪ (১০০’র মধ্যে) এবং অবস্থান ১৮০ দেশের মধ্যে ১৪৯তম, যা গত দুই দশকেরও বেশি সময়ে সবচেয়ে খারাপ অবস্থান। Transparency International এই স্কোরকে “খুবই গুরুতর দুর্নীতির সমস্যা” হিসেবে চিহ্নিত করেছে । আবার বিশ্ব বিচার প্রকল্পের (World Justice Project) আইনের শাসন সূচকে বাংলাদেশ ১৪২ দেশের মধ্যে ১২৭তম অবস্থানে রয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নিচের সারিতে (শুধু পাকিস্তান ও আফগানিস্তান পিছনে)। এসব পরিসংখ্যান দেশের বিদ্যমান সংকটের গভীরতাকে তুলে ধরে। এই প্রবন্ধে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের জ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট, ন্যায়বিচারের অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক অবস্থা, রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাহীনতা, নেতৃত্বের সংকট এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এ সকল সংকটের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি অংশে সাম্প্রতিক তথ্য ও নির্ভরযোগ্য উৎসের আলোকে সমস্যার বিবরণ ও তার পরিণতি উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।
জ্ঞানের অভাব ও শিক্ষাগত সংকট-
বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে অগ্রগতি সত্ত্বেও “জ্ঞানের অভাব” ও শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত সংকট একটি বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নামমাত্র ভর্তির হার উচ্চ (উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক স্তরে নেট ভর্তি হার ~৯৮% এর কাছাকাছি), কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান ও জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে। দেশের বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয় প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। ২০০০ সালে ঘোষিত ডাকার ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ জিডিপির ৬% শিক্ষা খাতে ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং UNESCO শিক্ষাখাতে কমপক্ষে জিডিপির ৪-৬% বিনিয়োগের সুপারিশ করে। কিন্তু বাস্তবে গত ২০ বছর ধরে শিক্ষাখাতে সরকারের ব্যয় জিডিপির ২% এর নিচেই রয়ে গেছে। অর্থবছর ২০১৬-২০২২ সময়ে বাংলাদেশ গড়ে জিডিপির মাত্র ১.৮% শিক্ষা খাতে ব্যয় করেছে, যা কম উন্নত দেশগুলোর মধ্যেও সর্বনিম্নদের একটি এবং এই সময়কালে ৩৫টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে বেশিরভাগই ২% বা তার বেশি বিনিয়োগ করেছে। তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশ ভারত শিক্ষা খাতে ২০২১ সালে জিডিপির ৪.৬% এবং পাকিস্তান ১.৭% ব্যয় করেছে। বাজেটে এই অপ্রতুল বরাদ্দের ফলে শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হয় না, অধিকাংশ অর্থ বেতন-ভাতা ইত্যাদি অরাজস্ব খাতে ব্যয় হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, প্রশিক্ষিত শিক্ষক, আধুনিক পাঠ্যক্রম ও উপকরণের অভাবে শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
শিক্ষার মানের সংকটের আরো একটি পরিমাপ হল সাক্ষরতার হার ও শিক্ষার্থীদের বাস্তব দক্ষতা। সরকারি হিসাবে দেশে সাধারণ সাক্ষরতার হার প্রায় ৭৪% (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যার) হলেও প্রকৃত কার্যকর সাক্ষরতার হার মাত্র ৬৩% এর কাছাকাছি। অর্থাৎ এখনো প্রায় ৩৭% মানুষ কার্যকরভাবে পড়তে ও লিখতে অক্ষম, যা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণে বড় বাধা। উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায়ও মান-সংকট স্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বহু শিক্ষার্থী শ্রমবাজারের চাহিদামতো দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না, ফলে বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান-সঙ্কট তীব্র হচ্ছে। বাংলাদেশে যুবসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষা বা কর্ম কোনোটিতেই নিযুক্ত নয়; সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৫-২৯ বছর বয়সী প্রায় ৪০% তরুণ-তরুণী বর্তমানে না কাজ করছে, না পড়াশোনা করছে, এই NEET (Not in Education, Employment or Training) যুবদের হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিএবং সাম্প্রতিক বছরেও প্রায় অপরিবর্তিত (২০২৩ সালে ৩৯.৯% যা আগের বছরের ৪০.৭% থেকে সামান্য কম)। এত বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম যুবসমাজ শিক্ষাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে থাকা দেশের জন্য এক গুরুতর সতর্কবার্তা। বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মাধ্যমে এই যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল খাতে না আনতে পারলে যাকে বলে “ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড” অর্থাৎ জনমিতিক বোনাস ক্লান্তি বা বিপর্যয়ে রূপ নিতে পারে। BIDS-এর মহাপরিচালক বিনায়ক সেন সতর্ক করেছেন যে, তরুণদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা না গেলে বাংলাদেশের জনমিতিক সুবিধা দুর্যোগে পরিণত হতে পারে । তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, “বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করার পর শিক্ষার্থীরা কী করছে, তা নীতিনির্ধারকদের খুঁজে বের করতে হবে,” অন্যথায় সমাজে বেকার ও হতাশ তরুণদের সংখ্যা বেড়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতে পারে। সারসংক্ষেপে, জ্ঞান ও শিক্ষার এই সংকট শুধু ব্যক্তিপর্যায়ে নয়, সামগ্রিকভাবে জাতির মানবসম্পদ উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবে গুণগত শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে ঘাটতি থাকায় ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও পেশাজীবী শ্রেণি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাচ্ছে না। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই রাখা এবং আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি গড়ে তোলায় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে।
ন্যায়বিচার সংকট-
বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতি এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সংকট বহুল আলোচিত একটি সমস্যা। আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি হলেও বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরণের চাপ ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে। বিশ্ব বিচার প্রকল্পের আইনের শাসন সূচক ২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৪২টি দেশের মধ্যে ১২৭তম অবস্থানে রয়েছে । সূচকটির বিভিন্ন উপসূচকে বাংলাদেশের দুর্বলতা বিশেষভাবে স্পষ্ট: মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২ দেশের মধ্যে ১৩৪তম এবং নাগরিক বিচার (Civil Justice) সূচকে ১৩২তম, যা ইঙ্গিত করে যে মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষা ও নাগরিকদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি খুবই পিছিয়ে আছে। এছাড়া সরকারী ক্ষমতার ওপর বাধানিষেধ (Constraints on Government Powers), দুর্নীতির অনুপস্থিতি, উন্মুক্ত সরকার (open government) প্রভৃতি মানদণ্ডেও বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় নিম্নস্তরে। অর্থাৎ শাসন কাঠামোতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা ও বৈষম্য প্রকট।
বিচার বিভাগের অন্যতম বড় সমস্যার একটি হল মামলাজট এবং ধীর ন্যায়বিচার, যা কার্যত ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চনার শামিল। দেশের বিভিন্ন আদালতে মামলার সংখ্যা বছরের পর বছর জমে থেকে পাহাড়সমান আকার নিয়েছে। ২০২২ সালের শেষে দেশের সর্বমোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল প্রায় ৪১,৯৬,৬০৩ । বিচারকের সংখ্যাগত অভাব এ সংকটের প্রধান কারণগুলোর একটি। আইন কমিশনের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশে প্রতি ৯৪,০০০ মানুষের জন্য মাত্র ১ জন বিচারক রয়েছেন । তুলনায় প্রতিবেশী ভারতে প্রতি ~৪৭,৬০০ জনে ১ জন এবং পাকিস্তানে ৫০,০০০ জনে ১ জন বিচারক আছেন । বিচারকের স্বল্পতার কারণে প্রতিটি বিচারককে গড়ে বহু শত মামলা একসাথে পরিচালনা করতে হয় – উচ্চ আদালতের একজন বিচারকের ওপর গড়ে প্রায় ৫,৭৪১টি মামলা এবং জেলা পর্যায়ের প্রতি বিচারকে প্রায় ২,০৩৩টি মামলার ভার পড়েছে। বিচারক সংকট, অবকাঠামো ঘাটতি ও প্রক্রিয়ার জটিলতায় বছরের পর বছর মামলার নিস্পত্তি না হওয়ায় ন্যায়বিচার পেতে জনগণকে অসহনীয় বিলম্ব মেনে নিতে হয়। প্রচলিত প্রবাদ আছে: “বিলম্বিত ন্যায়বিচার, ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হওয়ার সমতুল্য।” বাস্তবেও, বাংলাদেশে বিচার পেতে দীর্ঘসূত্রিতা ও অনৈতিক প্রভাব জনগণের আইনের শাসনের ওপর আস্থা কমিয়ে দিচ্ছে।
নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরেকটি অন্তরায় হচ্ছে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতার অভাব এবং বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির উপস্থিতি। আইন কমিশনের প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে যে বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা এখনো “সোনার হরিণ” রয়ে গেছে; রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সম্পন্ন হলেও বিচার বিভাগ তার প্রাপ্য গুরুত্ব ও স্বাধীনতা লাভ করেনি। রাজনৈতিক প্রভাব, ক্ষমতাসীনদের চাপ কিংবা দুর্নীতি অনেক ক্ষেত্রে বিচারিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ ঘটানোর অভিযোগ রয়েছে, ফলে ন্যায়বিচার বিপন্ন হয়। Transparency International Bangladesh (TIB) এর বিশ্লেষণে উঠে এসেছে যে দুর্নীতি ও অবিচার পরস্পরের সাথে জড়িত একটি বৃত্ত, যেখানে দুর্নীতি বিচারব্যবস্থাকে দুর্বল করে এবং দুর্বল বিচারব্যবস্থা আবার দুর্নীতিকে বাড়তে দেয়। যখন ঘুষ ও রাজনৈতিক প্রভাব বিচার অঙ্গনে প্রবেশ করে, তখন বিচার প্রক্রিয়া বিকৃত হয় – অপরাধীরা শাস্তি থেকে পার পেয়ে যায় আর ভুক্তভোগীরা ন্যায় থেকে বঞ্চিত হয়। ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সংস্কৃতি বিচারাঙ্গনে ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা জন্ম দেয়।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচারের সংকট পরিলক্ষিত হয়। একদিকে অপরাধ দমনে পুলিশের কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, অন্যদিকে আইনরক্ষকদের বিরুদ্ধেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে, যা সমান্তরালভাবে চলছে। সাম্প্রতিক কালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম,মব ও আদালতে নির্যাতনের ঘটনাবলী নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে জনগণের একাংশ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে উৎসাহী হচ্ছে যা সামাজিক অস্থিরতার লক্ষণ। দ্যা ডিপ্লোম্যাট সাময়িকীতে প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে: দেশে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর জনআস্থা নড়বড়ে হয়ে আছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সুযোগে গণপিটুনি ও গণসম্পৃক্ত সহিংসতা ঘটছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় দেখা গেছে, পুলিশ সদস্যদের জনতা আক্রমণ করে আসামি ছিনিয়ে নেওয়া বা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মতো চরম ঘটনা ঘটেছে। এটি স্পষ্টতই আইন ও বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থার অভাবের ইঙ্গিত দেয়, যা একটি সমাজের জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি।
সারকথা, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের বিদ্যমান সংকট বহুস্তরে বিস্তৃত – মামলা নিষ্পত্তির ধীরগতি ও জট, বিচারক স্বল্পতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতার অভাব, এবং আইন প্রয়োগকারীদের প্রতি জনবিশ্বাসের ঘাটতি। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে গণমানুষের আস্থা আরও কমে যাবে ও সামাজিক শৃঙ্খলা বিপন্ন হবে। আইন কমিশনের সতর্কবার্তাও উল্লেখযোগ্য: তারা বলেছে এ বিশাল মামলাজট দ্রুত কমানোর ব্যবস্থা না নিলে বিচার ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে এবং বিচার ব্যবস্থার ওপর জনবিশ্বাসও ধ্বসে পড়বে । ন্যায়বিচারহীনতার এই পরিবেশ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও আইন মেনে চলার মনোভাব থেকে বিমুখ করতে পারে, যা সুস্থ সমাজ গঠনের পথে বড় বাধা।
মূল্যবোধের অবক্ষয়-
সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বাংলাদেশের সামগ্রিক সংকটকে আরও ঘনীভূত করছে। ঐতিহ্যগতভাবে বাঙ্গালি সমাজ নীতিনিষ্ঠা, পারস্পরিক সম্মান ও মানবিক মূল্যবোধের জন্য পরিচিত হলেও সাম্প্রতিক দশকে বিভিন্ন স্তরে নৈতিকতার পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাড়তি দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, অসততা এবং সামাজিক সংহতির ঘাটতিতে। অন্যতম উদ্বেগজনক বিষয় হল যে দুর্নীতিগ্রস্ত আচরণ ও অনৈতিক কার্যকলাপ সমাজে ক্রমেই স্বাভাবিক বা মেনে নেওয়ার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যা জাতির নৈতিক ভিতকে দুর্বল করছে।
রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত দুর্নীতি ও অসৎ প্রচলনীতির উপস্থিতি নৈতিক অবক্ষয়ের একটি প্রধান চিহ্ন। Transparency International-এর তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে দুর্নীতি কেবল বিস্তৃতই নয়, ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিচ্ছে – সরকারি সেবাপ্রাপ্তি থেকে শুরু করে চাকরি ও শিক্ষাপ্রাপ্তি, সর্বত্র ঘুষ-স্বজনপ্রীতির সংস্কৃতি জনজীবনকে প্রভাবিত করছে। TIB-এর এক পর্যালোচনায় উঠে এসেছে, দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ও নেতৃত্বে এমন অনেক “নেতা” তৈরি হয়েছে যারা আদর্শ, মেধা ও সেবার মাধ্যমে নয় বরং হুমকি-ধমকি, অর্থবল, পরিবারগত পরিচিতি ও পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্কের জোরে টিকে আছেন। তারা সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি নয়, বরং যেসব গোষ্ঠী অর্থ ও পেশিশক্তি দিয়ে তাদের ক্ষমতায় এনেছে তাদের কাছে দায়বদ্ধ। পৃষ্ঠপোষকতা, সহিংসতা ও দলীয় আনুগত্যের এই নেটওয়ার্ক মেধা ও সৎ যোগ্যতার পরিবর্তে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করেছে, যেখানে যোগ্যতার বদলে ঘুষ-তদবিরই সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পরিণতিতে প্রশাসন ও রাজনীতিতে দক্ষতা ও নীতিবোধের ঘাটতি দেখা দিয়েছে; অকার্যকারিতা, দুর্নীতি আর সাধারণ মানুষের রাজনীতির প্রতি গভীর অবিশ্বাস প্রতিনিয়ত বাড়ছে। অর্থাৎ নেতৃস্থানীয়দের নৈতিক স্খলন পুরো সমাজকেই ভুল বার্তা দিচ্ছে যে দুর্নীতি যেন সফলতার পূর্বশর্ত।
মূল্যবোধের অবক্ষয়ের আরেকটি দিক হল সামাজিক স্তরে ন্যায়-নীতি ও সহানুভূতির অভাবজনিত ঘটনার বৃদ্ধি। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজে নৈতিক শিক্ষার ঘাটতির ফলস্বরূপ সহিংসতা, প্রতারণা, অন্যের অধিকার বা সম্পত্তির প্রতি অসম্মান ইত্যাদি ঘটনা বেড়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে শুরু করে পরীক্ষায় নকল বা গ্রেড কেনাবেচা-এর মতো ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সততার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রের এমন অনিয়ম শুধু ব্যক্তির নয়, সামগ্রিকভাবে জাতির নৈতিক মানদণ্ডকে নিচে নামাচ্ছে। একইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে ভেজাল ও ঠকবাজি, জালিয়াতি কিংবা ওজনে কম দেওয়া – এসব প্রবণতাও সমাজে নৈতিকতার সংকটের উদাহরণ। আইন প্রয়োগ দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেকেই শাস্তির ভয় না পেয়ে অনৈতিক পথকে লাভজনক হিসেবে দেখছে।
সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একটি মারাত্মক দিক হল পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে নীতি-নৈতিকতার উচ্ছ্বাস হ্রাস পাওয়া। নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি, তরুণ সমাজে মাদকাসক্তি ইত্যাদি সমস্যার উত্থান নৈতিক মূল্যবোধের দুর্বলতার সাথেও জড়িত। উদাহরণ হিসাবে, বাংলাদেশে এখনো শিশুবিবাহ একটি বড় সামাজিক সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। আইনত নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর প্রথা হিসেবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও বহু অভিভাবক নানাবিধ সামাজিক-আর্থিক কারণে কন্যাশিশুদের অল্প বয়সে বিয়ে দিচ্ছেন। সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ২০-২৪ বছর বয়সী বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে প্রতি দুইজনের একজন (প্রায় ৫০%) ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিবাহিত হয়েছিল। যদিও ২০১১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দেশে শিশুবিবাহের হার প্রায় ১৬% কমেছে, তবু এই হার এখনও দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চের মধ্যে রয়েছে এবং গ্রামীণ-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষত বেশি। এই পরিসংখ্যান ইঙ্গিত করে যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব এবং পুরনো প্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মেয়েশিশুর অধিকার ও ভবিষ্যৎ এখনও উপেক্ষিত হচ্ছে। এটি শুধু আইন লঙ্ঘনের বিষয় নয়, সমাজের নৈতিক মূল্যবোধেরও অবনতি নির্দেশ করে – যেখানে সাম্য, ন্যায্যতা ও শিশুদের প্রতি দায়িত্ববোধ এখনো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
এছাড়াও সাম্প্রতিক কিছু সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায়ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দৃশ্যমান হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে গুজব বা ধর্মীয় উস্কানিকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় ও বাড়িঘরে হামলার ঘটনা ঘটেছে, যা ঐতিহ্যগত ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির পরিপন্থী। এসব ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দুর্বল প্রতিক্রিয়া এবং দোষীদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া একদিকে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার অভাবকে তুলে ধরে, অন্যদিকে সামাজিকভাবে সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতিকে প্রকাশ করে।
সমষ্টিগতভাবে এসব উদাহরণ দেখায় যে, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতির স্থিতিশীলতা ও ঐক্যের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। দুর্নীতি এবং অসততা যখন সামাজিকভাবে প্রায় স্বাভাবিকীকৃত হয়, তখন নতুন প্রজন্মও সেই বিকৃত মূল্যবোধ আয়ত্ত করে ফেলতে পারে। এ থেকে একটি “দুষ্টচক্র” সৃষ্টি হয় – যেখানে দুর্নীতি বিচারহীনতা তৈরি করে আর বিচারহীনতা আবার দুর্নীতিকে বাড়িয়ে তোলে। মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে পরিবার থেকে রাষ্ট্র – সব পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষার প্রসার, আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরি; অন্যথায় ভবিষ্যৎ নাগরিকরা আদর্শ ও ন্যায়ের প্রতি বিশ্বাস হারাতে পারেন, যা জাতির সার্বিক উন্নয়নের অন্তরায় হবে।
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক অবস্থা-
উপর্যুক্ত সামাজিক, শিক্ষাগত, নৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটসমূহের প্রভাব সবচেয়ে গভীরভাবে পড়ছে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক অবস্থার ওপর। তরুণ ও যুবসমাজ, যারা আগামীর বাংলাদেশ গড়ার মূল চালিকাশক্তি, তারা এই নানামুখী সমস্যা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বড় হচ্ছে। এর ফলে তাদের মানসিক স্বস্তি, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ প্রভাবিত হচ্ছে। অনেক তরুণ-তরুণীর মনোজগতে তৈরি হচ্ছে হতাশা, ক্ষোভ ও অনাগ্রহ, যা দীর্ঘমেয়াদে জাতির জন্য অশনিসংকেত।
প্রথমত, বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান সংকট তরুণদের মধ্যে তীব্র হতাশা ও আত্মবিশ্বাসের সংকট তৈরি করছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উচ্চশিক্ষিতসহ বিপুল যুবসমাজ শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান উভয় ক্ষেত্রেই সুযোগের অভাবে NEET অবস্থায় রয়েছে। যারা উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করছেন তাদের মধ্যেও অনেকেই যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না, বা বহুদিন চাকরির অপেক্ষায় থাকছেন। দেশে যুব বেকারত্বের হার অফিসিয়াল পরিসংখ্যানে হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু “আন্তর্নিহিত বেকারত্ব” ও “অপ্রতুল চাকরি” একটি বড় সমস্যা। বিশেষত কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক চাপে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি মন্থর হয়েছে, অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ব্যবসা গুটিয়েছেন – যার প্রতিফলন তরুণদের ওপর পড়েছে। পেশাগত অনিশ্চয়তা ও আর্থিক অস্থিরতা তরুণদের মনে ভবিষ্যৎ নিয়ে একধরণের দ্বিধা ও নিরাপত্তাহীনতা জন্ম দিচ্ছে। বেশ কিছু তরুণ মাদকাসক্তি, অপরাধপ্রবণতা বা চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকিতে আছে – যার মূলে রয়েছে বেকার বসে থাকা ও জীবনে লক্ষ্য হারানোর অবস্থা। UNICEF-এর প্রতিবেদনসমূহ ইঙ্গিত করে যে শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (যেমন উদ্বেগ, বিষণ্ণতা) বাড়ছে, যার পেছনে শিক্ষাজীবনের চাপ, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও সামাজিক সহায়তার অভাব ভূমিকা রাখছে।
দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনাস্থা তরুণদের মানসিকতায় বিচ্ছিন্নতাবোধ ও অস্থিরতা তৈরি করছে। ক্রমাগত দুর্নীতি, বৈষম্য ও অবিচারের ঘটনাগুলো দেখে তরুণ সমাজ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা হারাচ্ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কয়েকটি জাতীয় নির্বাচনে বিরোধীদলের অংশগ্রহণ না করা, ভোট জালিয়াতি ও সহিংসতার অভিযোগ এবং স্বচ্ছতার অভাব তরুণ ভোটারদের একটি বড় অংশকে ভোটপ্রক্রিয়া থেকে বিমুখ করেছে। ২০২৪ সালের বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচনের পর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০০৮ সালের পর ভোটার হওয়া প্রজন্মের প্রায় ৭৫% তরুণ ভোটার জাতীয় নির্বাচনে কখনো ভোটই দিতে পারেনি (অংশ নেয়নি বা দিতে চাইলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে)। নির্বাচনগুলোর একপেশে ও সহিংস পরিবেশ, ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা ও কারচুপির অভিজ্ঞতা বহু নবীন ভোটারকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এই “ভোট না দেওয়া প্রজন্ম” দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনের প্রতি বেশ অনগ্রহ ও অবিশ্বাস পোষণ করে, যা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি শেখার ক্ষেত্রে নেতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে। যখন তরুণরা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তাদের মতামত বা ভোটের মূল্য নেই, তখন তারা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে সরে যায় – যা নাগরিক হিসেবে তাদের দায়িত্ববোধ ও সমাজের প্রতি সংযোগ কমিয়ে দিতে পারে।
তৃতীয়ত, বর্তমানে অনেক মেধাবী ও দক্ষ তরুণ তাদের ভবিষ্যৎ দেশ নয়, বিদেশে খুঁজছেন, যা “ব্রেন ড্রেইন” বা মেধাপ্রবাহ হ্রাসের সমস্যার সৃষ্টি করছে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, ক্যারিয়ার গড়ার সীমিত সুযোগ এবং নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি থেকে অনেক শিক্ষিত যুবক-যুবতী উন্নত শিক্ষার কিংবা চাকরির জন্য বিদেশে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে পাড়ি জমাচ্ছেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫ লাখ বাংলাদেশি কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দেন । ২০২০ সালে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭৪ লাখ। তাদের অধিকাংশই শ্রমিক শ্রেণির হলেও সাম্প্রতিককালে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যেও দেশত্যাগের প্রবণতা বাড়ছে। উন্নত জীবনযাত্রা, নিরাপত্তা ও কর্মক্ষেত্রে মূল্যায়নের আশায় অনেকেই পশ্চিমা দেশ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা পাশ্বর্বতী উন্নত অর্থনীতিগুলোতে স্থায়ী হতে চাইছেন। এই ধরণের মেধা ও পরিশ্রমী যুবসমাজের দেশত্যাগ ভবিষ্যতে দেশের জন্য দ্বিগুণ ক্ষতি ডেকে আনতে পারে: একদিকে দেশ দক্ষ জনশক্তি হারাচ্ছে, অন্যদিকে যারা দেশেই আছেন তাদের মধ্যেও অনুপ্রেরণার অভাব তৈরি হচ্ছে। তরুণ সমাজের এই “ক্ষয়” তাদের মানসিকতার ওপরও প্রভাব রাখে – বিদেশে স্থায়ী হতে না পারা বা দেশেই থেকে গুমরে মরার দোটানায় অনেকেই ভুগছেন।
চতুর্থত, উপরোক্ত সংকটগুলোর সম্মিলিত প্রভাবে যুবসমাজের মূল্যবোধ ও মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। যখন তারা চারদিকে অনিয়ম, অসততা ও অবিচার দেখে এবং ব্যক্তিগত উন্নতির পথকে সংকীর্ণ হিসেবে উপলব্ধি করে, তখন হতাশা, ক্রোধ বা নিরাশাবাদ সহজেই ঘিরে ধরে। British Council-এর Next Generation প্রতিবেদনের সর্বশেষ সংস্করণ (২০২৪) বলছে, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ ২০১৫ সালের তুলনায় কিছুটা কমেছে – ২০১৫ সালে যেখানে ~৬০% তরুণ দেশের গতিপ্রকৃতি “সঠিক পথে” মনে করত, ২০২৩ সালে সেই অনুপাত নেমে ~৫১% এ এসেছে। অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম যুবা দেশ নিয়ে আশাবাদী, বাকিরা হয় হতাশ নয়তো নিশ্চুপ। যদিও তরুণদের মানসিক দৃঢ়তা এবং প্রতিকূলতা জয় করার উদ্যম প্রবল, তবু বারবার একই ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে তাদের অনেকেই সমাজের প্রতি এক ধরনের বীতশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছে। এর ফলশ্রুতিতে কেউ কেউ সামাজিক আন্দোলন বা প্রতিবাদের পথে নেমে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করছেন – যেমন ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে কিশোর-তরুণদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পুরো পৃথিবী দেখেছে। আবার কেউ হয়ত ভিন্নভাবে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করছে – সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিদ্রূপাত্মক বা আক্রমণাত্মক মন্তব্যের মাধ্যমে, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে চরমপন্থী আদর্শের দিকে আকৃষ্ট হয়ে। এসবই মূলত একই উৎস থেকে উৎসারিত: নতুন প্রজন্ম এমন এক সমাজ চায় যেখানে মেধা ও পরিশ্রমের মর্যাদা আছে, ন্যায়বিচার ও সৎ মানুষের জয় হয়, এবং নিরাপদ-সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা থাকে। বর্তমান সংকটময় সমাজ বাস্তবতা সেই আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যাওয়ায় তাদের মানসিক জগতে দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ জন্ম নিচ্ছে।
সারসংক্ষেপে বলা যায়, দেশের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক দুরবস্থার ছায়া তরুণ প্রজন্মের মনে পড়েছে। যদি তারা এই সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন ও হতাশ হয়ে পড়ে, তবে জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব ও কর্মীশক্তি গড়ে উঠবে না। তাই আগামী প্রজন্মের মানসিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে, তাদের জন্য ন্যায্য ও সুযোগপ্রদানকারী পরিবেশ তৈরি করতে হবে – যেখানে তারা স্বপ্ন দেখতে ও তা পূরণে চেষ্টা করতে পারবে। তা না হলে দেশের বড় সম্পদ এই যুবশক্তি বিষাদ, অবিশ্বাস ও নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয়ে পড়বে, যা জাতীয় উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বিপত্তি হয়ে দাঁড়াবে।
রাষ্ট্রের প্রতি আস্থার অভাব-
রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শাসনব্যবস্থার প্রতি জনগণের বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের আস্থাহীনতা বাংলাদেশের বর্তমান সংকটকে আরও ঘনীভূত করছে। গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থার মৌলিক শর্ত হল নাগরিকদের রাষ্ট্রের উপর আস্থা রাখা এবং রাষ্ট্রেরও নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। কিন্তু বাংলাদেশে ঘুষ-দুর্নীতি, জবাবদিহিতার ঘাটতি, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন এবং সেবা খাতে ব্যর্থতার কারণে এক ধরণের বিশ্বাসের সঙ্কট তৈরি হয়েছে। এই আস্থাহীনতা কেবল রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সকল পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায়।
নির্বাচনী ব্যবস্থা ও শাসন কাঠামোয় অনাস্থা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৯৬ সাল থেকে বাংলাদেশে পরপর কয়েকটি জাতীয় নির্বাচন বিতর্কিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য বা ছিলই না, এবং ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ওঠে। এর ফলে সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে সুশীল সমাজ – অনেকের মনেই নির্বাচন ও সরকার গঠন প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন জন্মেছে। বিশেষ করে ২০১৪, ২০১৮ ও সর্বশেষ ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, জাল ভোট, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, বিরোধী প্রার্থীদের দমন-পীড়ন ইত্যাদি ঘটনা ঘটে এবং টার্নআউটও ছিল ইতিহাসের নিচুগুলোর একটি। এসব ঘটনার প্রভাব তরুণদের ওপর আলাদাভাবে পড়েছে – যারা স্বাধীনতার পর জন্ম নিয়েও কোনো সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেনি। ক্রমাগত এমন প্রহসনের নির্বাচনে অনেক নাগরিকের মতেই “ভোট দিয়ে কি হবে” মনোভাব জন্মেছে, যা রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ এবং আস্থাকে ভীষণভাবে ঝাঁকুনি দিয়েছে। গণতন্ত্রের প্রাথমিক ধাপ ভোটদান ও সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধনে যাদের আস্থা হারিয়ে গেছে, তারা রাষ্ট্রের অন্যান্য দিকগুলোতেও নিস্পৃহ বা বৈরাগী হয়ে ওঠে।
প্রশাসন ও সেবা খাতেও জনগণের আস্থার সংকট স্পষ্ট। ব্যাপক দুর্নীতির কারণে সরকারি দপ্তর, ভূমি প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, কর ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষের মনে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত ‘ঘরোয়া দুর্নীতি জরিপ’ সমীক্ষাগুলোতে বারবার উঠে এসেছে যে পুলিশ, আদালত, ভূমি অফিস, পাসপোর্ট অফিস প্রভৃতি সেবা খাতগুলোতে ঘুষ ছাড়া কাজ করা দুষ্কর এবং এসব খাতকে জনগণ সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে দেখে। যখন জনগণ মনে করে যে ন্যায্য কোনও সেবা পেতে হলে নিয়ম মেনে আবেদন করে লাভ নেই, বরং ঘুষ বা চেনাজানার মাধ্যমে কাজ আদায় করতে হবে – তখন রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আস্থা কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু, যেসব সংস্থা দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে (যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন) তারাই যদি রাজনৈতিক প্রভাবাধীন ও আজ্ঞাবহ থাকে, তখন এই অনাস্থা আরও বাড়ে। Transparency International Bangladesh উল্লেখ করেছে যে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে “শূন্য সহনশীলতা” ঘোষণা করলেও ২০২০-২০২৩ সময়ে কোনো কার্যকর কৌশল নেওয়া হয়নি; বরং দুর্নীতিগ্রস্তদের লুটপাটের টাকা বিদেশে পাচার জারি থেকেছে এবং জবাবদিহির দাবি এলে তা উপেক্ষা বা স্থগিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ – যেমন ACC (দুদক) – রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত না হওয়ায় ঘুষ-দুর্নীতি অব্যাহত থেকেছে এবং স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ প্রশাসনকে কলুষিত করছে । এসব চিত্র জনগণের রাষ্ট্রচর্চায় আস্থা নষ্ট করে এবং নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সামাজিক চুক্তি দুর্বল হয়।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচার বিভাগের প্রতিও আস্থাহীনতা ক্রমশ বাড়ছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, হেফাজতে নির্যাতন, হত্যা ইত্যাদি অভিযোগ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে র্যাব ও পুলিশের কিছু কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ও সমালোচনার মুখে পড়েছে, যা দেশের অভ্যন্তরেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে। জনগণের বড় অংশ চায় নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার; কিন্তু যখন তাঁরা দেখেন অভিযোগ করেও প্রভাবশালী অপরাধীরা শাস্তি পাচ্ছে না, বরং উল্টো ভুক্তভোগীরাই হয়রানির শিকার হচ্ছে – তখন সাধারণ মানুষের আইনের শাসনের ওপর আস্থা হারিয়ে যায়। এর পরিণতিতে কেউ কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে প্ররোচিত হয়, যা আগের অধ্যায়ে বর্ণিত গণপিটুনির ঘটনা বৃদ্ধি ইত্যাদি থেকে স্পষ্ট। আবার অনেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করেন। সামগ্রিকভাবে, প্রশাসন ও আইনরক্ষাকারী সংস্থাগুলোর প্রতি অনাস্থা মানে হল রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোর প্রতি অনাস্থা।
এই আস্থাহীনতা শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয়; এর আন্তর্জাতিক মাত্রাও রয়েছে। Freedom House-এর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সূচকে বাংলাদেশ বর্তমানে “আংশিক মুক্ত” (Partly Free) দেশের তালিকায় এবং Economist Intelligence Unit-এর গণতন্ত্র সূচকে “হাইব্রিড রেজিম” (অর্থাৎ অধঃপতিত গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মিশ্রণ) হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মূল্যায়নেও বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা আদর্শ গণতন্ত্রের মান অর্জনে ব্যর্থ। টিআইবি উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশ নিজেকে “হাইব্রিড রেজিম” ক্যাটাগরিতে ফেললেও দুর্নীতি সূচকে তার স্কোর ওই শ্রেণির গড় (৩৬) থেকে ১২ পয়েন্ট কম এবং অনেক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের চেয়েও খারাপ (কর্তৃত্ববাদী শ্রেণির গড় ২৯-এর তুলনায় বাংলাদেশ ২৪)। এমনকি যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো (যেমন উত্তর কোরিয়া) রয়েছে, সেই গোষ্ঠীর মধ্যেও বাংলাদেশের দুর্নীতির পরিস্থিতি প্রায় তলানির দিকে। এই তুলনাগুলো বোঝায় যে শাসন ও ন্যায়পরায়ণতার বিচারে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে, যা তার নাগরিকদের কাছে এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে দুর্বল করছে। জনগণ যখন দেখে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও দেশের সুশাসনের ঘাটতি নিয়ে উদ্বিগ্ন, তখন তাদের নিজের দেশের ব্যবস্থার প্রতিও আস্থার অভাব বাড়ে।
রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাহীনতার আরও একটি ফল হল সামাজিক সংহতি ও চুক্তির ভঙ্গুরতা। রাষ্ট্র যখন জনগণের চাহিদা ও অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না, তখন নাগরিকরা বিকল্প ব্যবস্থার দিকে ঝোঁকে – যেমন বেসরকারি উদ্যোগ, আত্মকেন্দ্রিকতা, বা প্রবাসে পাড়ি জমানো। দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়বদ্ধতার চেতনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি ছোটবেলা থেকেই দেখে যে “আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য – কোনও কিছুতেই রাষ্ট্রের ভরসা নেই”, তবে তারাও বড় হয়ে রাষ্ট্রকে এড়িয়ে চলাকে কৌশল হিসেবে নেবে। এ অবস্থায় দেশ গঠনে জনগণের অংশগ্রহণ কমে যায় এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের দেয়াল উঁচু হতে থাকে।
নিষ্পত্তিযোগ্যভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের প্রতি আস্থার অভাব বাংলাদেশের প্রকৃত অগ্রগতির পথে একটি গভীর অন্তরায়। এই আস্থাহীনতা দূর করতে হলে রাষ্ট্রকে তার শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে – সুশাসন, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা প্রদান করে। তা না হলে আস্থাহীনতার এই বিষবৃক্ষ ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট ডেকে আনতে পারে।
নেতৃত্বের সংকট-
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে নেতৃত্বের সংকট একটি বহুল আলোচিত বিষয়, যা দেশের সামগ্রিক সংকটকে আরও জটিল করে তুলছে। যোগ্য, দূরদর্শী ও নৈতিক নেতৃত্বের অভাবের কারণে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ ও পরিচালনায় দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। নেতৃত্বের এই সংকট কেমন এবং কেন – তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এটি মূলত রাজনৈতিক সংস্কৃতি, দলীয় কাঠামো ও সমাজের রুচিগত সমস্যার সাথে জড়িত।
প্রথমত, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি প্রায় অদল-বদল করে দু’টি প্রধান রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্বেই থেকে এসেছে এবং উভয় দলের নেতৃত্বই মূলত পরিবারকেন্দ্রিক ও দীর্ঘকাল ধরে অপরিবর্তিত। বিগত তিন দশকের বেশি সময় ধরেই রাষ্ট্র ক্ষমতা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির হাতেই পালাবদল করছে, এবং দুটি দলের নেতৃত্বে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু পরিবার ও জিয়া পরিবারের সদস্যরা। দলীয় অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চা কম থাকায় নতুন নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সীমিত ছিল। দলের ভিতরে তোষামোদ ও আনুগত্য পুরস্কৃত হয়েছে, কিন্তু মেধা, নতুন ধারণা বা বিরোধিতা দমিয়ে রাখা হয়েছে – যার ফলে ভবিষ্যতের জন্য দক্ষ নেতৃত্বের পাইপলাইন তৈরিই হয়নি। এই ধারায় দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেত্রী এবং বিএনপি নেত্রী উভয়ই সত্তরোর্ধ্ব; তাদের পরের প্রজন্মের নেতৃত্ব কে হবে তা অনিশ্চিত। আওয়ামী লীগ বা বিএনপির অভ্যন্তরে কোন নবীন/মাঝারি স্তরের নেতা গণমানুষের মাঝে সমান গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন বলে উদাহরণ কম। ফলে যেদিন বর্তমান শীর্ষ নেতৃত্ব অযোগ্য হবেন বা সরে যাবেন, সেদিন হয় দলগুলো ভেঙে পড়বে নয়তো অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিপর্যস্ত হবে – উভয়ই রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার জন্য অশনি সংকেত। সম্প্রতি এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনকালে আওয়ামী লীগ সরকারের সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) ভাবমূর্তিও ক্ষয়প্রাপ্ত এবং শেখ হাসিনার প্রস্থান-পরবর্তী আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ দলীয়ভাবে উত্তরসূরি গড়ে না তোলার সংস্কৃতি নেতৃত্বের সঙ্কটকে ঘনীভূত করছে। এবং সেই জায়গাটি দখল করে নিয়েছেন প্রতিক্রিয়াশিল সার্থান্নাসি চক্র।
দ্বিতীয়ত, নেতৃত্বের মান ও গুণাবলীর এক অবনমন পরিলক্ষিত হচ্ছে – অনেক নেতা আছেন, কিন্তু আদর্শবান ও জনকল্যাণে নিবেদিত নেতার সংখ্যা খুব কম। স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতার লাভের জন্য ধনবল ও দুর্বৃত্তবল ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। The Daily Star-এ প্রকাশিত এক মতামতে বিশ্লেষক লিখেছেন: “দশক দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে এমন নেতা-কমীরা প্রাধান্য পেয়েছেন যারা দূরদর্শিতা বা সেবা দিয়ে নয়, বরং ভয়-ভীতি, সম্পদ, পারিবারিক পরিচয় ও পৃষ্ঠপোষকতার জাল বিস্তার করে এগিয়েছেন। দল ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা স্থানীয় সন্ত্রাসী ও মাসলম্যানদের পেছনে দাঁড়িয়ে আইন ভঙ্গ করতে সহায়তা করেছে। এ ধরনের নেতারা সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি নন, বরং যাদের কল্যাণে তারা ক্ষমতায় এসেছেন তাদের কাছেই বাধ্য। এই পৃষ্ঠপোষকতার নেটওয়ার্ক মেধাকে উপেক্ষা করে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করছে। ফলে এ ধরনের “নেতারা” আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে শিক্ষা, দৃষ্টি বা নীতিগত ভিত্তি দরকার তা থেকে বঞ্চিত – বরং তারা টিকে থাকেন গুজব রটনা, বিভেদ সৃষ্টি ও জনমন ভুল পথে চালিত করার মাধ্যমে। ফলাফল? অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও সাধারণ মানুষের রাজনীতির প্রতি গভীর অবিশ্বাস।” এই বিশদ চিত্রদেশনায় স্পষ্ট যে বর্তমানে যে “নেতা” হিসেবে পরিচিতদের অনেকেই আদতে জনকল্যাণের নেতৃত্ব নয় বরং সড়যন্ত্র, বাহুবল-ধনবলের সমীকরণে উপরে উঠেছেন। সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধানে তাঁদের নেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান, পরিকল্পনা বা আন্তরিকতা। উপরন্তু, এ ধরনের নেতৃত্ব রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকলে নিজেদের গোষ্ঠী বা স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সুবিধা করে দিতে ব্যস্ত থাকে; জনসেবার নৈতিকতা ও দূরদর্শিতা অনুপস্থিত থাকে।
তৃতীয়ত, তরুণ নেতৃত্বের অভাব ও নেতৃত্ব বিকাশে প্রতিবন্ধকতা নেতৃত্ব সংকটকে দীর্ঘায়িত করছে। যে দেশে জনসংখ্যার সিংহভাগ তরুণ, সেখানে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তরুণদের প্রতিনিধিত্ব অত্যল্প। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোতে ছাত্র ও যুব সংগঠন থাকলেও সেগুলো প্রায়শই ক্রীড়ানক বা চাপসৃষ্টির টুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কার্যকর নেতৃত্ব তৈরির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নয়। অনেক মেধাবী ও আদর্শবাদী তরুণ রাজনীতিতে যোগ দিতে আগ্রহ হারাচ্ছে, কারণ রাজনীতির পরিবেশ দুর্বৃত্তায়ন ও কালিমাচ্ছন্ন। টাকা–পয়সা খরচ করে দলের পদ কেনা, ক্ষমতা প্রদর্শনে লিপ্ত থাকা, বড় নেতার আশীর্বাদ পেলে টিকে যাওয়া – এ সংস্কৃতিতে নীতিনিষ্ঠ ও আদর্শবাদী নতুন নেতা উঠে আসা কষ্টকর। ফলে নেতৃত্বের জগতে একধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা পূরণ করছে সুযোগসন্ধানী ও অবদানহীন মানুষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিবর্তনের জন্য আমাদের নেতৃত্বের সংজ্ঞা ও মানদণ্ড পরিবর্তন করতে হবে। এতদিন শক্তি ও শাসনকে যেভাবে “ক্ষমতা” হিসেবে দেখা হয়েছে – অর্থাৎ কর্তৃত্ব, দমন, বিত্তের জোর – সেটি পাল্টে সহমর্মিতা, জ্ঞান, সততা ও ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতাকে নেতৃত্বের গুণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তা না হলে আমরা একই “Strongman” সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি দেখতে থাকব যা জাতিকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।
নেতৃত্বের সংকট শুধুই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; সামাজিক, শিক্ষাগত, পেশাগত সর্বক্ষেত্রেই ভালো নেতার অভাব টের পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে নজর দিলে দেখা যায়, অনেক vice-chancellor বা প্রশাসক দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পেয়ে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত, সেখানে শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা ও অগ্রগতি নিশ্চিতের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। বেরোজগারত্ব সমাধানে, দুর্নীতিমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান চালাতে বা জনবান্ধব সেবা পৌঁছাতে দক্ষ নেতৃত্ব প্রয়োজন – কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্য লোক সামনের কাতারে নেই। মূল্যবোধের অবক্ষয় ও দলীয়করন এর আগের অংশে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও সমানে প্রযোজ্য – বরং নেতৃত্বের গুণমানের অবক্ষয় মানেই সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়।
এই সংকটের ফলে ভবিষ্যতের জন্যও নেতৃস্থানীয় আসনে উপযুক্ত মানুষ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণ, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দরকার সুবিবেচক, সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব – যেটার ঘাটতি এখন প্রকট। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দক্ষ নেতৃত্বের অভাব বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনা, শ্রমিক অধিকার বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনায় নিজ দেশের স্বার্থ রক্ষায় আমাদের নেতাদের সক্ষমতা প্রয়োজন। সেখানে যদি মৌলিক জ্ঞান বা কুশলতার অভাব থাকে, তবে বাংলাদেশ লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করবে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশের অতীতে সুনাম ছিল; এখন দেশ উন্নয়নশীল পর্যায়ে যাওয়ার পর সেই মান বজায় রাখতে শক্তিশালী নেতৃত্ব দরকার, নতুবা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশ মার্জিনালাইজড হয়ে যেতে পারে।
পর্যালোচনায় বলা যায়, বাংলাদেশের নেতৃত্বের সংকট একটি শেকড়মূল সমস্যা, যেটি অন্য সকল সংকটকেই প্রশ্রয় দেয়। দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, শিক্ষার সংকট – এসবই সমাধানযোগ্য যদি সদিচ্ছা ও দক্ষ নেতৃত্ব থাকে। তাই নেতৃত্বের মানোন্নয়ন ও প্রজন্মান্তর হওয়ার পথ সুগম করা এখন সময়ের দাবি। এ জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা, নতুনদের সুযোগ দেয়া, স্বচ্ছ মনোনয়ন প্রক্রিয়া ও প্রার্থী বাছাইয়ে মেধা-সততা অগ্রাধিকার – এসব সংস্কার করতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থাতেও সিভিক শিক্ষা ও নেতৃত্ব বিকাশের ওপর জোর দেয়া জরুরি। তা নাহলে পুরোনো ষড়যন্ত্র, পরিবারতন্ত্র ও পেশিশক্তির আধিপত্য অব্যাহত থাকলে “পুরনো দানবের হাতেই দেশ পড়ার” আশঙ্কা থেকে যাবে। বাংলাদেশের জনগণ অবশ্যই উত্তম নেতৃত্ব ডিজার্ভ করে, যারা গড়ে, ভাঙে না; সেবা করে, লুটপাট নয়; ঐক্যবদ্ধ করে, বিভক্ত নয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ ঘটাতে না পারলে এই ধরনের নেতার উত্থানই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি বয়ে আনতে পারবেনা।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট-
বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটসমূহের অভিঘাত ও বহিঃপ্রকাশ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও প্রতিফলিত হচ্ছে। বৈশ্বিক বিভিন্ন সূচক ও তুলনামূলক পরিমাপে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে সুশাসন, ন্যায়বিচার, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, মানব উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশটি তার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীদের তুলনায় কোথায় দাঁড়িয়ে। এসব সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর গভীরতা বুঝতে সাহায্য করে।
গণতান্ত্রিক শাসন ও মানবাধিকার সূচকে বাংলাদেশ বেশ পিছিয়ে আছে। বিশ্ব বিচার প্রকল্পের আইনের শাসন সূচকে (Rule of Law Index) বাংলাদেশ ২০২৪ সালে ১৪২ দেশের মধ্যে ১২৭তম অবস্থানে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার ৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪র্থ – কেবল আফগানিস্তান ও পাকিস্তানই বাংলাদেশ থেকে পিছনে, আর নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভারত এগিয়ে। Transparency International-এর দুর্নীতির ধারণা সূচক (CPI) ২০২৩ অনুযায়ী ১৮০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯তম এবং স্কোর ২৪, যা বৈশ্বিক গড় (৪৩) থেকে অনেক কম এবং ২০১২ সালের পর সবচেয়ে নিচু স্কোর। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সর্বনিম্নের দিক থেকে দ্বিতীয় – শুধু আফগানিস্তানের স্কোরই বাংলাদেশ থেকে খারাপ, ভুটান অঞ্চলটিতে সেরা (স্কোর ৬৮) এবং ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান – সবার স্কোর বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ভালো, অর্থাৎ দুর্নীতির বিপরীতে লড়াইয়ে বাংলাদেশ তার প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে এবং বিশ্বদরবারে আমাদের স্থান প্রায় তলানির দিকে। প্রেস স্বাধীনতা সূচকেও (Reporters Without Borders এর World Press Freedom Index) আমাদের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। ২০২৩ সালের সূচকে বাংলাদেশ ১৮০ দেশের মধ্যে ১৬৩তম স্থান পেয়েছিল – যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন (এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানেরও নিচে) বর্তমান অবস্থাতো আরো ভয়াবহ। সরকার ও ক্ষমতাসীনদের সমালোচনার অধিকার সীমিত করা, মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ ও সংবাদকর্মীদের হেনস্থা/গ্রেফতার প্রভৃতির কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশের মিডিয়া পরিস্থিতিকে খারাপ থেকে খারাপতর বলেই চিহ্নিত করেছে।
অবশ্য সব সূচকেই যে বাংলাদেশ পিছিয়ে তা নয়; জনকল্যাণমূলক কিছু সূচকে বাংলাদেশের উন্নতি ও আঞ্চলিক তুলনায় ভালো করাও লক্ষ্য করা যায়। মানব উন্নয়ন সূচকে (Human Development Index) বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নতি ধরে রেখেছে। UNDP-এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে ২০২১-২২ সালে বাংলাদেশের এইচডিআই মান ছিল ০.৬৬১, এবং ১৯১ দেশের মধ্যে স্থান ছিল ১২৯তম – যা “মাঝারি মানব উন্নয়ন” ক্যাটাগরিতে পড়ে। দক্ষিণ এশিয়ার গড় HDI (০.৬৩২) থেকে বাংলাদেশ সামান্য এগিয়ে আছে এবং পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের তুলনায় অনেক ভালো অবস্থানে, যদিও শ্রীলঙ্কা ও ভুটানের চেয়ে পিছিয়ে আছে। এ দিক থেকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয়ের কিছু সূচকে বাংলাদেশ ধারাবাহিক অগ্রগতি দেখিয়েছে – যেমন গড় আয়ু, শিশুমৃত্যু হার, নারী শিক্ষা ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। তবে একই সাথে অসমতা-সমন্বয়কৃত HDI-তে অসমতার কারণে আমাদের ২৩.৯% অর্জন কমে যায়, যা আঞ্চলিক কিছু দেশের তুলনায় বেশি এবং দেশে আভ্যন্তরীণ বৈষম্যের দিকটি সামনে আনে। লিঙ্গসমতা সূচকেও (Gender Inequality Index) বাংলাদেশের অবস্থান ২০২১ সালে ১৩১তম, যা লিঙ্গ বৈষম্যের গুরুতর চিত্র তুলে ধরে। অর্থাৎ, মানব উন্নয়ন সূচকে সামগ্রিক অগ্রগতি সত্ত্বেও লিঙ্গ ও আয়ের বৈষম্য এবং মানবসম্পদ ব্যবহারে ঘাটতি রয়ে গেছে, যা উন্নত দেশ হওয়ার পথে চ্যালেঞ্জ।
আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের এই পারফরম্যান্সের প্রতিফলন আমরা বৈদেশিক সম্পর্কেও দেখতে পাই। উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলো ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সফল একটি উদাহরণ হিসেবে বহু বছর ধরেই প্রশংসা করে আসছিল, বিশেষত দারিদ্র্য বিমোচন, জনস্বাস্থ্য ও নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে গণতান্ত্রিক অবক্ষয় ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কিছুটা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ওপর জোর দিচ্ছে এবং নতুবা বাণিজ্যিক সুবিধা (যেমন জিএসপি) বা নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারিও দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-এর কয়েকজন কর্মকর্তার উপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে – যা স্পষ্ট বার্তা দেয় যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সংকটগুলো সম্পর্কে অবগত এবং উদ্বিগ্ন। আবার, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের বড় ভূমিকা থাকায় বিশ্বমঞ্চে আমাদের সুনাম রয়েছে; তবে সেখানেও ভবিষ্যতে আভ্যন্তরিন মানবাধিকার রেকর্ড বিবেচনায় আসতে পারে।
আন্তর্জাতিক তুলনায় বাংলাদেশের এই অবস্থান আমাদের ভবিষ্যৎ কৌশলের ব্যাপারেও ইঙ্গিত দেয়। ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে, যেখানে সুশাসন ও স্বচ্ছতা বিনিয়োগ আকর্ষণের পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থার “Ease of Doing Business” রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে নিম্ন – এর পেছনে বুরোক্রেসি, দুর্নীতি, অবকাঠামো দুর্বলতা ইত্যাদি কারণ। এসব মোকাবিলা না করতে পারলে এলডিসি উত্তরণের পর বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রফতানিতে চ্যালেঞ্জ আসবে। একইভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) পূরণেও সুশাসনের সূচক (১৬ নম্বর লক্ষ্য) একটি বড় বিষয়, যেখানে বাংলাদেশের উন্নতি প্রয়োজন।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট থেকে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি শিক্ষা হল: আমাদের প্রতিবেশী ও অনুরূপ দেশগুলো কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে, কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে – সেসব দেখে নিজেরা শিখতে পারা। উদাহরণস্বরূপ, ভুটান দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় সেরা অবস্থানে রয়েছে; নেপাল সাম্প্রতিক সময়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা আনায় আইনের শাসনে আঞ্চলিক সেরা হয়েছে। আবার শ্রীলঙ্কা অর্থনৈতিক দুর্নীতির মাশুল দিয়ে আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। পাকিস্তানে ধারাবাহিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক প্রভাব তার উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে। এই আঞ্চলিক উদাহরণগুলো বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা স্বরূপ – যদি দুর্নীতি ও শাসন সংকট সমাধান না করা হয়, তাহলে অর্থনৈতিক সাফল্য টেকসই নাও হতে পারে, বরং হঠাৎ সংকটে বিপর্যস্ত হতে পারে। অন্যদিকে, সুশাসন নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশ উন্নয়ন পথ আরও মসৃণ হবে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও অধিক মর্যাদা পাবে।
সার্বিকভাবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক সূচক ও প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংকটের প্রতিচ্ছবি বহন করে। অর্থনৈতিক অর্জন সত্ত্বেও সুশাসন, ন্যায়বিচার ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের দুর্বলতা বৈশ্বিকভাবে চিহ্নিত। এই অবস্থায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংকট নিরসন জরুরি – যা না করলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারে এবং কূটনৈতিক চাপের মুখে পড়বে। তবে ইতিবাচক দিক হলো: আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ও উন্নয়ন অংশীদাররা বাংলাদেশকে সহায়তা দিতে ইচ্ছুক, যদি আমরা সুশাসন ও মানবাধিকারের প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় থাকি। আত্মসমালোচনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার দুর্বল দিকগুলো ঠিক করে নিলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব দুটোই বৃদ্ধি পাবে। তবে সংস্কার হতে হবে সামগ্রিক ভাবে জাতীর ইচ্ছার প্রতিফলন হিসাবে, কারো বা কোনো নিদৃষ্ট গোষ্ঠির লক্ষ্য বাস্তবায়নে নয়।
সর্বপরি-বাংলাদেশের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক সংকটসমূহ পরস্পর জড়িত একটি জটিল অবস্থা তৈরি করেছে, যা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও জাতি গঠনে গভীর প্রভাব ফেলছে। জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব আমাদের মানবসম্পদ উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে, ন্যায়বিচারের সংকট আইনের শাসনে ফাটল ধরাচ্ছে, মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল করছে, তরুণ প্রজন্ম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও হতাশ হচ্ছে, রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাহীনতা প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা নড়বড়ে করছে, আর নেতৃত্বের সংকট ভবিষ্যতের পথচলায় অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে। এই বহুমাত্রিক সংকট অগ্রাহ্য করার মতো নয় – কারণ জাতির অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতার জন্য এটি একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের সৃষ্টিলগ্নে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার অন্যতম ভিত্তি ছিল একটি ন্যায়ভিত্তিক, শিক্ষিত ও শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরেও আমরা যদি সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে থাকি, তবে এটি আত্মসমালোচনার সময় বটে।
আশার কথা হলো, বাংলাদেশের জনগণ অত্যন্ত সহনশীল, পরিশ্রমী ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন। গত কয়েক দশকে আমরা দারিদ্র্য কমানো, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য দেখিয়েছি। ঠিক একইভাবে, সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটগুলোও দূর করা অসম্ভব নয়, যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সামাজিক আন্দোলন একযোগে কাজ করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দমনে বাস্তব পদক্ষেপ, শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিচার বিভাগের সংস্কার, নৈতিক শিক্ষার প্রসার এবং যুবসমাজের ক্ষমতায়ন – এই দিকগুলোতে মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে এখন বিনিয়োগ করা জরুরি; অন্যথায় বর্তমানের এই সংকটপূর্ণ পরিবেশেই আমাদের সন্তানদের বেড়ে উঠতে হবে, যা জাতির সম্ভাবনাকে খর্ব করবে।
বাংলাদেশ ২০২৬ সালে এলডিসি তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হতে যাচ্ছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জনকে লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছে। এই বৃহৎ লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন একটি কার্যকর, ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে জনগণের আস্থা থাকবে এবং আগামী প্রজন্ম নিরাপদ বোধ করবে। দেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ – সঠিক দিকনির্দেশনা ও পরিবেশ পেলে তারাই বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে সম্মানিত অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যদি আমরা তাদের একটি ভঙ্গুর সমাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা এবং মূল্যবোধহীন পরিবেশ দিয়ে বড় করি, তবে তারা সেই বোঝা টেনেই ক্লান্ত হয়ে যাবে।
দেশের অগ্রগতি ও শান্তিময় ভবিষ্যৎ গঠনের প্রয়াসে সরকার, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকলের সম্মিলিত ভূমিকা দরকার। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও স্বাধীন গণমাধ্যম নিশ্চিত করতে হবে, যাতে সমস্যা আড়ালে না থেকে জনসমক্ষে আসে এবং সমাধানে চাপ তৈরি হয়। দুর্নীতি ও অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতা বাড়াতে হবে। সর্বোপরি, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে জনগণের মনের ভাষা বুঝে সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত, প্রশাসনে স্বচ্ছতা আরোহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ – এসব কোনো বিলাসিতা নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য আবশ্যক বিনিয়োগ। যেমনটা একজন অর্থনীতিবিদ বলেছেন, “মানুষের উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ খরচ নয়, ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ”। আমাদেরও মানবসম্পদ ও সুশাসনে এখন বিনিয়োগ করতে হবে।
পরিশেষে, সংকটগুলো যত গভীরই হোক, সঠিক দিকনির্দেশনা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সেগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। বাংলাদেশের ইতিহাস সাক্ষী যে আমরা ঘুরে দাঁড়াতে জানি। সামাজিক আন্দোলন, যেমন ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন – প্রতিবারই তরুণ প্রজন্ম দেশকে এগিয়ে নিতে মূল ভূমিকা রেখেছে। এখন সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, ন্যায়ভিত্তিক ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ গড়ে তোলার। এই লক্ষ্য পূরণে আমাদের সমাজের প্রতিটি অংশকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংস্কার ও পরিবর্তনের পথে হাঁটতে হবে। আগামী দিনের বাংলাদেশ সেই দেশ হোক যেখানে জ্ঞানের আলো, ন্যায়ের শাসন ও সুস্থ মূল্যবোধে উজ্জ্বল একটি প্রজন্ম জাতিকে নেতৃত্ব দেবে, এবং যেখানে নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাশীল থেকে মিলিতভাবে জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করবে। এতেই আমাদের মহান স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সম্ভাবনার পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।
সঙ্কট চিহ্নিত করা হয়েছে, করণীয়ও কমবেশি জানা – এখন প্রয়োজন সুদৃঢ় রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও জাতির উন্নত স্বপ্ন বাস্তবায়নের স্বার্থে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং পরিবর্তন ঘটাতে হবে, যাতে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই একটি মর্যাদাপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

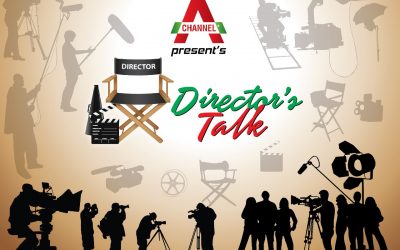

0 Comments